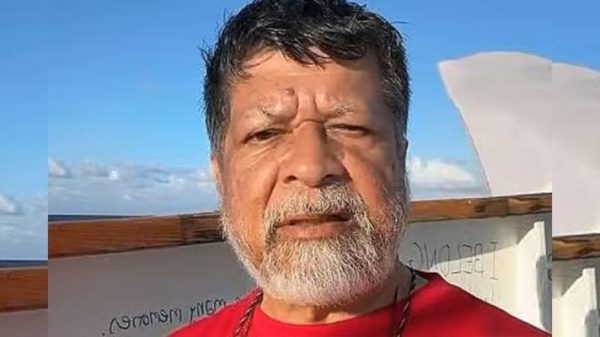বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১:২৬ পূর্বাহ্ন
মহামারী, ভয়ের সংস্কৃতি এবং মৃত্যুর রাজনীতি

সায়েমা খাতুন:
এক. করোনা মহামারী বিদেশ থেকে ঢুকে পড়ার আগে আমরা যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম। আমরা কি করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে পারতাম না? মানুষের গণ-মৃত্যুর আশঙ্কাকে কি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে পারতাম না? আমরা উদ্যমে ও পরিশ্রমে আবার অর্থনীতির মোড় ফেরাতে পারব, কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে হারিয়ে ফেলা বাবা-মা-ভাই-বোন-সন্তানকে আর কোনো কিছুর বিনিময়েই কোনো দিন ফিরে পাব না। মহামারীতে এই নিদারুণ মৃত্যুগুলো কি রোধ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল? সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করে কি মৃত্যুকে ন্যূনতম করা যেত না? আমার সহজ সাদামাটা প্রশ্ন করোনা মহামারী কি মধ্যযুগের প্লেগ, উপনিবেশকালের বসন্ত, কলেরা, ওলাওঠার মতো নিবারণ অযোগ্য ছিল? এটা কি মধ্যযুগ, যখন মানুষ ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স তো দূরের কথা, কেন মানুষের মড়ক লেগেছে তাও বুঝতে পারত না, ঈশ্বরের অভিশাপ মনে করত। যদি তা না হয়, তাহলে মানুষকে বাঁচানোর জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করা হয়েছে কি? করোনার বিস্তার রোধে সরকার, চিকিৎসা স্বাস্থ্য প্রশাসন, মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিয়েছে কি? এমনকি মোটামুটি সন্তোষজনক পদক্ষেপ নিয়েছে কি? বিশেষজ্ঞসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের পরামর্শ আমলে নিয়েছে কি? না। উপরন্তু, এই জীবন-মরণের গুরুদায়িত্বশীল পদে কর্মরত ব্যক্তিদের অসংলগ্ন কথাবার্তা, মিথ্যাচার ও কর্মকাণ্ড অবিশ্বাস ও অনাস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের হাতে এই মহামারী নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্যাকসিন ছাড়া জনস্বাস্থ্যের আরও অনেক কৌশলই তো ছিল! অথচ ঘরে ঘরে আজ মৃত্যুভয়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আজ এমন কেউ নেই যে, একবার হলেও আজরাইলকে মনে করেনি, মৃত্যুর চিন্তায় ভূতগ্রস্ত হয়নি। মহামারীতে অকাল অস্বাভাবিক এই মৃত্যুকে আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। কিছুদিন আগে যেমন ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ায় মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিলাম, ভুল চিকিৎসার কিংবা চিকিৎসার অভাবে, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে আমরা মেনে নিয়েছিলাম। বিষ মেশানো খাদ্য, ক্রসফায়ার, গুম-খুন, ধর্ষণ, পুড়িয়ে মারা, গণপিটুনিতে মারা, বন্যায় ভেসে, লঞ্চডুবিতে, ভিআইপি কর্র্তৃক জনসাধারণের চলাচলের ফেরি আটকানোয় অ্যাম্বুলেন্সে শিশুর মৃত্যু রোজকার জীবনে বিচিত্রভাবে জনসাধারণের মৃত্যুকে বাংলাদেশে নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়া চলছে অগণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।
দুই. আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার একটি কাঠামোগত কৌশল মৃত্যুর রাজনীতি। ইতালীয় দার্শনিক গিয়র্গি আগামবেন মৃত্যুর গ্রিক দেবতা থানাটোসের নাম অনুসরণে একে নাম দিয়েছেন ‘থানাটোপলিটিক্স’ (১৯৮৫)। নাগরিকের দেহের ওপর, জীবন-মরণের ওপর আধুনিক যুক্তিশীল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুঁকো বলেছেন জৈব-রাজনীতি বা বায়ো-পলিটিক্স। জৈব-রাজনীতি হলো, অসংখ্য ও বিচিত্র কলাকৌশলে জনগণের দেহ-প্রাণ ও জনসংখ্যার ওপর আধিপত্য কায়েম করা (ফুঁকো, যৌনতার ইতিহাস, ১৯৭৬, পৃ. ১৪০), যেমন রাষ্ট্র কর্র্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, টিকা নিতে বাধ্য করা, গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেওয়া, জনস্বাস্থ্য বিধানে, মহামারী নিয়ন্ত্রণে নাগরিকের দেহের ওপর বিভিন্নভাবে কর্র্তৃত্ব প্রয়োগ করা ইত্যাদি। এই জৈব-রাজনীতির ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আগামবেন কাছাকাছি আরেকটি ধারণা নিয়ে আসেন মৃত্যুর রাজনীতি বা থানাটোপলিটিক্স। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম ও বিস্তারে মৃত্যুর ব্যবহারকে তিনি বলেন থানাটোপলিটিক্স। এই থানাটোপলিটিক্সের ধারণা আজকের বাংলাদেশে গণ-মৃত্যুর বিস্তার বুঝতে ভীষণ কাজের। এর সাহায্যে আমরা বুঝতে পারব, কেন বাংলাদেশের মতো দেশে গণহারে মৃত্যুর কোনো জবাবদিহি নেই? কেন প্রতিদিন অকাল অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুকে জাতীয় (এবং বৈশ্বিকও) জীবনের অঙ্গ করে তোলা হয়েছে? কীভাবে এই নির্বিকারত্ব টিকে আছে? কীভাবে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় ও বশ্য হয়ে পড়েছে? আর আমরা এই ব্যাপারে কি-ই-বা করতে পারি? রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে খরচযোগ্য করে তোলার সংস্কৃতি আজকে নতুন নয়, কয়েক দশক ধরে বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই রাজনীতির মরণ খেলা। গণতন্ত্রহীন শাসননীতি এবং বলপ্রয়োগের ক্ষমতা, ভিন্নমতের দমন-পীড়নের রাজনীতি মৃত্যুকে স্বাভাবিক ও নিত্যদিনের করে তুলেছে, অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের সংস্কৃতি হয়ে পড়েছে। আমরা ধরেই নিয়েছি, ঘুম থেকে উঠে কোনো না কোনো প্রিয়জনের অকাল মৃত্যুসংবাদ শুনতেই পারি। যে কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে নিরাপদে বাড়ি নাও ফিরতে পারে। আমরা নিজেরাও মনে মনে ঘরে অথবা বাইরে অকালে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি যেন। আমাদের রক্ত অনেক আগেই ভয়ের সংক্রমণে দূষিত হয়ে গেছে, স্বাধীন মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা হিসেবে আমরা আর বেঁচে নেই। ব্যক্তি হিসেবে, নাগরিকরা এই সংস্কৃতির শিকার হয়ে গেছে, মৃত্যুর রাজনীতিতে আবিষ্ট ও বশীভূত হয়ে পড়েছে। তাই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যু দেখে কোনো রকম মর্মপীড়া ছাড়াই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারছে। প্রতিবেশীকে করোনায় মরতে দেখে তার পরিবারকে একঘরে করে ফেলছে, দাফন-কাফন করতে বাধা দিচ্ছে, সন্তান মাকে জঙ্গলে ফেলে এসেছে। আমজনতা একদিকে রাষ্ট্রের ওপর ভরসা হারিয়েছে, আবার অন্যদিকে হারিয়েছে নিজের সক্রিয় এজেন্সি এবং সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতা। হারিয়েছে নৈতিক বল দয়া, মায়া, করুণা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি, সংহতি ও সংঘবদ্ধতার মতো শক্তিশালী মানবিক গুণাবলি। পরস্পরকে সুরক্ষা প্রদানের সামাজিক চুক্তি ভেঙে নৈরাজ্যের রাজ্যে জীবন্মৃত এক বি-মানবিক সমাজে আমরা দিন গুজরান করছি। নিষ্ক্রিয়তা ও বিচ্ছিন্নতার ফাঁদে পড়ে এখন উপায়ন্তরহীনভাবে পরিত্রাণের জন্য ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করে নিরাকার ওপরওয়ালার নাম জপ করা ছাড়া যেন আর কিছু বাকি নেই। এই ভয়, আতঙ্ক, গণ-মৃত্যু নিয়ে নিষ্ক্রিয়তা সীমিত আকারের গণতন্ত্রের রাষ্ট্রে নিও-লিবারেল শাসনের অপকৌশল।
তিন. করোনা মহামারীতে এই পুরনো থানাটো-রাজনীতি নজিরবিহীন এক মহাদানবীয় রূপ ধারণ করেছে। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম যে, সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব সমানভাবে সব নাগরিকের জীবনরক্ষাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। আমরা ইতিহাসের সাক্ষী রইলাম যে, রাষ্ট্রযন্ত্র নাগরিকের জীবনের হেফাজতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেনি। করোনা মহামারী নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় নীতির দৃষ্টিভঙ্গিতেই দুর্নীতিগ্রস্ত পরগাছা ভিআইপি শ্রেণিকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বেশুমার জনতাকে কাতারে কাতারে মৃত্যুর দিকে অবশ্যম্ভাবীভাবে ঠেলে দেওয়া হলো। ভিআইপিদের আলাদা হাসপাতাল, ভেন্টিলেটর, অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে, অতি দ্রুতগতিতে চড়া মূল্যে করোনা চিকিৎসার ওষুধ বিক্রির অনুমতি দিয়ে ধনিক-মালিকদের জীবনের মূল্য গরিব কৃষক-শ্রমিকের চেয়ে বেশি ধরা হয়েছে। গণতন্ত্র ভিআইপিতন্ত্রে অধঃপতিত হয়েছে। জনগণ করোনা আক্রান্ত হয়ে মরবে, অ-করোনা রোগে চিকিৎসা না পেয়ে মরবে, চাকরি হারিয়ে না খেয়ে মরবে, ত্রাণ না পেয়ে অনাহারে-অপুষ্টিতে মরবে, জেল খেটে মরবে বা ডিজিটাল বাক-পরাধীনতায় মরবে, বিষাদরোগে মরবে যেভাবেই মরুক, মরতে তাকে হবেই। যদি নাই মরে, এই নির্লজ্জ মনুষ্যত্ববিহীন বেঁচে থাকাই এক গোটা প্রজন্মকে চির অপরাধী করে রাখবে। ঘরে ঘরে প্রিয়জনের মৃত্যুর শোক-বিলাপের মধ্যে, অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে এক মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণায় মরমে মরে বেঁচে থাকবে এরা। নিজের চোখের দিকে তাকাতে না পেরে মাথা নিচু করে বেঁচে থাকার এক বিষম লজ্জা টুঁটি চেপে ধরবে!
চার. মানুষকে কিংবা মানুষের অর্থনীতিকে বাঁচানোর এই অক্ষমতা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাণরক্ষাকারী কোনো গবেষণায় গত কয়েক দশকে কোনো বিনিয়োগ করা হয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অণুজীব, প্রাণ-রসায়ন, ফার্মেসি, জনস্বাস্থ্য এই বিভাগগুলো আছে কেন? এই বৈশ্বিক মহাসংকটেই যদি কোনো টেস্ট কিট, ভ্যাকসিন, কন্টাক্ট ট্রেসিং, মহামারী নিয়ন্ত্রণের কোনো কৌশলই আবিষ্কার করতে না পারল, তবে এরা আছে কেন? নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান যদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটকালে সহিংসতা নিরোধ করে সমাজের সংহতি রক্ষার কোনো উপায়ই বাতলে দিতে না পারল, বৈষম্যরেখা বিলোপে কোনো নির্দেশনা দিতে নাই পারল, অর্থনীতি যদি মন্দা সামলানোর রূপরেখা দেখাতে ব্যর্থই হলো, তবে এসব বাগাড়ম্বরে ভরা লেকচারসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর দরকার কী? করোনা মহামারী শুধু দুর্নীতি ও লোভগ্রস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেই উদোম করে দেয়নি, এসব নিষ্কর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউলিয়াপনাকেও উদোম করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল উদ্যমী গবেষকদের দলীয় রাজনীতির অপকৌশলে কোণঠাসা করে রাখার ফলে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থবিরতা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।
পাঁচ. আমাদের প্রথমে এই মৌলিক সামাজিক সম্মতিতে পৌঁছাতে হবে যে, প্রত্যেক জীবন অমূল্য। কেননা আমরা কেউ কখনো জীবন সৃষ্টি করতে পারব না। প্রত্যেকটি মানুষ অপ্রতিস্থাপনযোগ্য, বিনিময় অযোগ্য সম্পদ, জাতির জন্য স্রষ্টার অমূল্য উপহারস্বরূপ। মানুষের মৃত্যু কোনো সংখ্যা নয়, বিশ্বের মৌলিক রহস্য হলো প্রাণের সৃষ্টি এবং পরিসমাপ্তি। আমরা একে জানার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ভেদ করতে পারি না। একজন মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিংবা জাতীয় মহামারী ও সংক্রামক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান কিংবা জীবনের ওপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও জৈব-রাজনীতির জ্বালানি কাঠ নয়। সবকিছু মনে রাখা হবে। সবকিছু লিখে রাখা হবে। যে সন্তানের চোখের সামনে বাবা ভেন্টিলেটরের অভাবে শ্বাসকষ্টে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করল, সেই সন্তানদের চোখের পানিতে নতুন মহাভারত রচিত হবে। এক একজন মানুষ জাতির সমগ্র ইতিহাসের মালায় গাঁথা এক একটি অনন্য গল্প, যে গল্পের শেষ নেই। প্রত্যেকটি মানুষ এক অবিস্মরণীয় পারিবারিক-সামাজিক স্মৃতির মণিহার, মৃত বেওয়ারিশ লাশের নম্বর মাত্র নয়। সে অনেক সাধনায় জন্মানো কোনো মায়ের সন্তান, সে কারও পিতা এক বটবৃক্ষের ছায়া, সে ভায়ে-মায়ের স্নেহের সুঘ্রাণ। হয়তো সে একজন নেতা, কবি, গায়ক, প্রেমিক, দার্শনিক। প্রত্যেকটি মানুষের জীবন হলো অনন্ত সম্ভাবনা ও অসীম স্বপ্নের সসীম প্রতিরূপ। জীবন নিয়ে অবহেলা অধর্ম, অনৈতিক এবং সুস্পষ্টভাবে অপরাধমূলক আচরণ। কিন্তু জীবিতরা মৃতদের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। আমরা যারা বেঁচে আছি তারা কোনো না কোনোভাবে স্বজনদের প্রত্যেকটি অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায়দায়িত্ব বহন করি। আজ পর্যন্ত যারা বেঁচে রয়েছি, মহামারীর পর যারা বেঁচে থাকব, মৃতদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো মানবতার বিরুদ্ধে এই অপরাধগুলোকে চিহ্নিত ও উন্মোচন করা। সেটাই হবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম। মৃতদের সম্মান করার আচার-আনুষ্ঠানিকতা থেকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সভ্যতার সূচনা করেছিল। মৃতরা জীবিতদের শেকড়-বাকড়। মৃতদের স্মৃতিস্তম্ভের ওপরই রচিত হয় ইতিহাস। আর তা না হলে কীসের জাতি, কীসের নাগরিক, কার উন্নতি? মৃতদের মর্যাদা না দিয়ে জীবিতদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বৈধতাই থাকে না। বেঁচে আছি বলে যতক্ষণ শ্বাস আছে আমাদের এই থানাটোপলিটিক্সকে উন্মোচন করতে মগজ খাটানোর কাজ করে যেতে হবে। নিষ্কর্মা অপদার্থ নিষ্ক্রিয় পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে।লেখক
সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
sayemakhatun@juniv.edu